EastBengalPro
FULL MEMBER
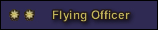
- Joined
- Jun 3, 2014
- Messages
- 690
- Reaction score
- 0
- Country
- Location

চীনের ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’: বাংলাদেশের লাভক্ষতি ১
বুনো রাজহাঁসের বৈশ্বিক উড়াল
বিংশ শতক ছিল আমেরিকার, একবিংশ শতক হবে কার? তা নির্ভর করছে যে প্রকল্পের সম্ভাবনার ওপর, তার অনেক নাম। একে প্রথমে ডাকা হচ্ছিল নয়া রেশমপথ (সিল্ক রোড) নামে। পরে বলা হলো ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড (ওবর)। কিন্তু ‘ওয়ান’ বা ‘একক’ কথাটার মধ্যে একাধিপত্যের লক্ষণ থাকায় এর সর্বশেষ নাম দেওয়া হয়েছে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ, সংক্ষেপে বিআরআই। একুশ শতাব্দী চীনা শতাব্দী হবে কি না, তা নির্ভর করছে এই বৈশ্বিক বাণিজ্য অবকাঠামো নির্মাণে সফলতার ওপর। তিনটি বৃহৎ এখানে এক হয়েছে: সবচেয়ে বেশি রাষ্ট্র, সবচেয়ে বড় অর্থায়ন ও সবচেয়ে বেশি জনসমষ্টি। বলা হচ্ছে, এটিই হতে যাচ্ছে আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক প্রকল্প। ৬৮টি দেশ, ৬০ শতাংশ বিশ্ব জনসংখ্যা এবং ৪০ শতাংশ উৎপাদন নিয়ে এই নয়া রেশমপথ রচনা করছে এশীয় আদলের নতুন বিশ্বায়ন।
চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের ডাকে ১৪-১৫ মে–তে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিআরআই ফোরামের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি এ প্রকল্পকে ‘বুনো রাজহাঁসের’ সঙ্গে তুলনা করেন। এই পাখি কেবল এশিয়াতেই পাওয়া যায়, ইউরোপে নয়। সি চিন পিং তাঁর বক্তৃতায় বলেন, বুনো রাজহাঁস ঝড় ও বাতাসের মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত নিরাপদে উড়তে পারে। কারণ, তারা ওড়ে ঝাঁক বেঁধে এবং একটা দলের মতো একে অন্যের পাশে থাকে। চীনের দাবি, এটা সহযোগিতার মাধ্যমে যৌথভাবে লাভবান হওয়ার নতুন এক মডেল। ভারত অবশ্য অভিযোগ করেছে, এটা নতুন ধরনের উপনিবেশবাদ, এটা দুর্বল রাষ্ট্রকে ঋণের জালে বেঁধে ফেলবে। তবে সবাই স্বীকার করছেন, এই শতাব্দীর সব থেক বড় উন্নয়ন প্রকল্প এটাই।
পুরোদমে বাস্তবায়িত হওয়া শুরু হলে বিআরআই হয়ে উঠবে বিশ্বায়ন ২.০। তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ৯০ দশকের গোড়ার বিশ্বায়নকে বলা হচ্ছে বিশ্বায়ন ১.০। আর এটা ঘটছে এমন সময়ে, যখন পশ্চিমা বিশ্বায়ন নিজের ভেতর থেকেই বাধার মুখে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ব্রিটেনে ব্রেক্সিটের বিজয় বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের ধারণার সমালোচনা করে আবার ফিরিয়ে আনছে জাতিরাষ্ট্র ও জাতীয় বাজারের ধারণা। এ রকম সময়ে চীনা বিশ্বায়ন বিশ্বের সামনে নিয়ে এসেছে নাটকীয় সম্ভাবনার চ্যালেঞ্জ। চীনের নেতৃত্ব কতটা উচ্চাভিলাষী হয়ে উঠেছে, এই কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রকল্প তার প্রধান উদাহরণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিধ্বস্ত ইউরোপকে পুনর্গঠনে ‘মার্শাল প্ল্যান’ যুক্তরাষ্ট্রকে দিয়েছিল পৃথিবীর শীর্ষ শক্তির স্বীকৃতি। সে সুবাদেই আমেরিকা বলতে ভালোবাসে, বিশ শতক হলো আমেরিকান শতক। কিন্তু মার্শাল প্ল্যান ছিল কেবল ইউরোপের বিষয়, আর বেল্ট অ্যান্ড রোড এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকাকে ধারণ করলেও এর আওতায় আসবে সারা পৃথিবীর বাণিজ্যই।
বিআরআই দৃশ্যত যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অঞ্চল ও করিডর প্রতিষ্ঠার প্রকল্প। সমালোচকদের মতে, তা আসলে চীনা পুঁজিবাদের বৈশ্বিক বিস্তারের পদক্ষেপ। এটা নেওয়া হয়েছে চীনের ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে। একদিকে শতবর্ষের নীরবতা ভেঙে চীন আপন সীমানার বাইরে ভূরাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের নীতি নিয়েছে, অন্যদিকে কয়েক দশকের মধ্যে এই প্রথম চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে দেখা দিয়েছে ধীরগতির লক্ষণ। পাশাপাশি দেশটির উৎপাদনক্ষমতা যত বেশি, তত বেশি রপ্তানি না হওয়ার সংকটও ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। বিআরআই হয়তো এসব সমস্যা কাটিয়ে ওঠারই চেষ্টা। পাশাপাশি তা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতির জন্য হাজির করেছে অভূতপূর্ব সম্ভাবনাও।
বিআরআইয়ের মূল চাবিশব্দ হলো কানেকটিভিটি। এর উদ্দেশ্য এশিয়াকে বিশ্ব বাণিজ্যের কেন্দ্রীয় ইঞ্জিন করে তোলা। এ পরিকল্পনায় থাকছে সমুদ্রপথে একগুচ্ছ আন্তর্জাতিক বন্দর, ভূমিতে আন্তসীমান্ত সড়ক, উচ্চগতির রেলপথ, বিমানবন্দর এবং ডিজিটাল যুক্ততার অবকাঠামো নির্মাণ। এর সমান্তরালে থাকবে বিদ্যুতের গ্রিড, গ্যাসের পাইপলাইন এবং বাণিজ্য–সহায়ক আর্থিক কার্যক্রম। এই বাণিজ্যপথ এশিয়ার বিস্তৃত এলাকায় জালের মতো ছড়িয়ে থাকবে, এশিয়াকে ভূমি-সমুদ্র-আকাশ ও ডিজিটাল মাধ্যমে ইউরোপ ও আফ্রিকার সঙ্গে যুক্ত করবে। চীনা রাষ্ট্রের সব স্তর, সব প্রাদেশিক সরকার এবং গণমাধ্যম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা মহলকে এই মহাপরিকল্পনা তৈরি ও তার বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে যুক্ত করা হয়েছে। প্রধান প্রধান রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংক নিচ্ছে এর অর্থায়নের মূল দায়িত্ব।
৩০টি দেশের সরকারপ্রধানসহ ১০০ দেশের প্রতিনিধির যোগদানের ঘটনায় বেইজিংয়ের দুদিনব্যাপী বিআরআই ফোরামের সম্মেলন হয়ে উঠেছিল নতুন সিল্ক রোড জাতিসংঘ। গোলটেবিলের আসন এবং সবার জন্য মাইক্রোফোন খোলা রেখে প্রেসিডেন্ট সি বোঝাতে চেয়েছেন, উদ্যোগ চীনের হলেও অংশীদারত্ব সবার, লাভের ভাগও সবার। চীনের তিন প্রতিদ্বন্দ্বীর দুটি, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান বেইজিংয়ে প্রতিনিধি পাঠালেও অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত অনুপস্থিত ছিল। এ শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক সম্মেলনে ভারতের না থাকা বড় প্রশ্ন হয়ে উঠেছে অনেকের কাছে। বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও মিয়ানমার এই সম্মেলনে উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল পাঠালেও ভারতের বিরাগ দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতিতে সৃষ্টি করছে নতুন উদ্বেগ।
ভারতের আপত্তির কারণ হিসেবে দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তরের বিবৃতিতে বলা হয়েছে সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকির কথা। ভারত মনে করে, বিআরআইয়ের অংশভুক্ত চীন-পাকিস্তান ইকোনমিক করিডরে (সিপিইসি) পাকিস্তানের অংশভুক্ত কাশ্মীর থাকায় তা ভারতের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি সৃষ্টি করছে। উল্লেখ্য, ভারত সমগ্র কাশ্মীরকেই তার সার্বভৌম অধিকারের অংশ বলে মনে করে। জবাবে ভারতের চীনা দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন লিউ জিংসং বলেন, সিপিইসির কাশ্মীরের ভেতর দিয়ে যাওয়াই যদি ভারতীয় বন্ধুদের বেল্ট অ্যান্ড রোডে যোগদানের ইচ্ছার বাধা হয়, তাহলে তাঁদের এই উদ্বেগ দূর করা যেতে পারে। ভারতের আরও ভয়, বিআরআই বাস্তবায়িত হলে ভারত-নিয়ন্ত্রিত ভারত মহাসাগরে চীনের প্রভাব অনেক বাড়বে।
অনেক ভারতীয় বিশ্লেষকও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এই ‘একলা চলো’ নীতির সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। দেশটির প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং বিজেপির সাবেক প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ির (১৯৯৯-২০০৪) উপদেষ্টা সুধীন্দ্র কুলকার্নি মনে করেন, ভারতের এই সিদ্ধান্ত ‘অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও আত্মঘাতী’। তিনি মনে করেন, বিআরআই ভারতের ব্যবসা, কর্মসংস্থান ও আন্তর্জাতিক অবস্থানকে শক্তিশালীই করবে। সুধীন্দ্র কুলকার্নি ভারতের বেসরকারি প্রতিনিধি হিসেবে বিআরআই সম্মেলনে অংশ নেন।
ইতিহাসে দেখা গেছে, পরাশক্তি হয়ে ওঠার কালে কোনো কোনো দেশের বিশেষ কোনো সুবিধা বা ক্ষমতার জন্ম হয়েছে, তা দিয়ে ওই সব দেশ বিশ্বকে দীর্ঘ সময়জুড়ে প্রভাবিত করতে পেরেছে। ব্রিটেন জাহাজ নির্মাণ ও নৌচালনা জ্ঞান দিয়ে সাম্রাজ্য গড়েছিল, যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পুঁজি ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা দিয়ে ইউরোপ পুনর্গঠন করে পাশ্চাত্যের নেতা হয়েছিল। পাশ্চাত্য তার অর্থনৈতিক ও প্রাযুক্তিক ক্ষমতা দিয়ে বিশ্বায়নের প্রথম পর্বের বাস্তবায়ন করেছিল। চীনের সেই বিশেষ সুবিধার দুটি দিক হলো, অবকাঠামো নির্মাণে চীনের বিশ্বসেরা দক্ষতা এবং বিরাট অঞ্চলজুড়ে অবকাঠামো নির্মাণে তাদের আর্থিক সামর্থ্য। চীন গত চার বছরে প্রকল্পভুক্ত দেশগুলোয় ইতিমধ্যে ৫০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে এবং বাড়তি আরও ৮৯০ বিলিয়ন ডলার ধাপে ধাপে ব্যয় করা হবে। এর বড় অংশটাই বিনিয়োজিত হবে উন্নয়নশীল দেশের যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণে।
উদীয়মান অর্থনীতি এবং জ্বালানি ও অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ ক্ষুধার্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এর দ্বারা কতটা উপকৃত হবে, কীভাবে ভূরাজনৈতিক জটিলতা ও বাধাগুলোকে কূটনৈতিক কৌশল ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে সমাধান করা হবে; এসবই আজকের বাংলাদেশের সামনে বড় প্রশ্ন হিসেবে হাজির হয়েছে।
চীনের ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’: বাংলাদেশের উন্নয়নের সন্ধিক্ষণ ২
বেল্ট অ্যান্ড রোড (বিআরআই) ফোরামের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়া ২৯ জন রাষ্ট্রনেতার মধ্যে বাংলাদেশের কেউ ছিলেন না। বাংলাদেশ পাঠিয়েছিল মন্ত্রী–মর্যাদার প্রতিনিধিদল। অথচ ভারত ছাড়া দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আর সব দেশের অংশগ্রহণ ছিল শীর্ষ পর্যায়ের। এ সম্মেলনে বাংলাদেশ মাত্র দুটি চুক্তি সই করেছে। কিন্তু গত বছরের শেষাশেষি চীনের প্রেসিডেন্টের ঢাকা সফরের সময় স্বাক্ষরিত ২৭টি চুক্তিকে আমলে নিলে বোঝা যায়, বিআরআই বিষয়ে বাংলাদেশ এগিয়েই আছে। এবারে সম্পাদিত ওই দুটি চুক্তির অধীনে চীন বাংলাদেশে শিল্প ও বাণিজ্য যোগাযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি জ্বালানি-উৎপাদন উচ্চপর্যায়ে নেওয়া, তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ, কয়লাখনির আধুনিকীকরণ এবং গাড়ির টায়ারের কারখানা প্রকল্পেও অর্থায়ন করবে। এসবই চীনের নয়া সিল্ক রোড কর্মসূচির খণ্ড খণ্ড অংশ।

বিআরআই ফোরামে বাংলাদেশের শীর্ষ নেতৃত্বের অনুপস্থিতিকে এ প্রকল্পে ভারতের আপত্তির প্রতিক্রিয়াজনিত সতর্কতা হিসেবেই দেখছেন বিশ্লেষকেরা। বিপরীতে চীনের কৌশল ছিল ‘শতাব্দীর বৃহত্তম প্রকল্পের’ পক্ষে বৈশ্বিক সমর্থন প্রদর্শন করা। রুশ নেতা ভ্লাদিমির পুতিন, তুর্কি নেতা রিসেপ এরদোয়ানসহ ছিলেন ২৯ জন রাষ্ট্রনেতা। এ ছাড়া ১০০ দেশের প্রতিনিধি এবং জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাসহ বিশ্বব্যাংক, এডিবি, আইআইবির মতো বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এতে যোগ দেয়। এসবই চীনের অর্থনৈতিক-কূটনীতির সক্ষমতার প্রমাণ। শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী, মিয়ানমারের অং সাং সু চি, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট এবং নেপালের উপপ্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ বুঝিয়ে দেয়, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রেশমপথে চীন মোটেই নিঃসঙ্গ পথিক নয়। ভারত বিআরআই ফোরামের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে।
ভারত মহাসাগরে চীনের অন্যতম প্রবেশপথের দেশ হিসেবে বিআরআই প্রকল্পে বাংলাদেশের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ যতটা, ততটাই ঝুঁকিপূর্ণ। বাংলাদেশি অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য তাই জোর দিয়েছেন ভারসাম্যের নীতির ওপর। তাঁর মতে, ‘চীনের এই উদ্যোগে বাংলাদেশের জড়িত হওয়াকে বৃহত্তর চিন্তার আলোকে দেখতে হবে। ভূরাজনৈতিক কারণে এসব প্রক্রিয়া ঝুঁকিও সৃষ্টি করে।’ দেশের শীর্ষ নীতি-গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির এই বিশেষ ফেলো বলেন, ‘আমাদের দুই পাশে দুই বৃহৎ প্রতিবেশী। এই দুই শক্তির দ্বন্দ্বের সুযোগ আমরা নিতে চাইছি। এটা থেকে যাতে আমরা আহত না হয়ে বেরিয়ে আসতে পারি, তা দেখতে হবে। এর জন্য দক্ষতা, দূরদৃষ্টি এবং কূটনৈতিক প্রজ্ঞা দরকার।’
বাংলাদেশ ইতিমধ্যে বেশ কটি বহুমাত্রিক বাণিজ্যিক ও যোগাযোগপ্রক্রিয়ার অংশ। বিবিআইএম, বিবিআইএন, বিমসটেকের কথা বলা যায়। এগুলো মূলত পণ্য পরিবহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্র। বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমারের মধ্যে অর্থনৈতিক করিডর (বিসিআইএম) বিদ্যমান থাকলেও ভারত-চীনের দ্বন্দ্বে এগুলোর কোনোটাই বাস্তবায়িত হতে পারছে না। বিসিআইএমের অধীনে কক্সবাজার-কুংমিং সড়ক তৈরি হলে তা চীন-মিয়ানমার-বাংলাদেশের পণ্য চলাচল সহজ করে দেবে। কিন্তু ‘ভারত চায় না এটা বাস্তবায়িত হোক। তাই তারা কক্সবাজার-কুংমিং সড়কের প্রস্তাবকে সিলেটের দিকে নিতে চাইছে। অথচ আমাদের কুংমিং হয়ে মিয়ানমার হয়ে চীনে পণ্য নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দরকার’, বলছিলেন চীনে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত আশফাকুর রহমান।
ভারতের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কের ঢালাই শক্তিশালী করার যে কৌশল চীন নিয়েছে, ভারত কি তা সহজভাবে নেবে? ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকর মন্তব্য করেছেন, ‘কানেকটিভিটির উদ্যোগ ও কৌশলগত স্বার্থের পারস্পরিক যোগাযোগ আমাদের উপমহাদেশে খুবই দৃশ্যমান। এই বাস্তবতার প্রতি আমরা উদাসীন থাকতে পারি না...।’ ভারত ইতিমধ্যে আগের ‘লুক ইস্ট’ বা পূর্বমুখী কূটনীতি থেকে ‘অ্যাক্ট ইস্ট’ অর্থাৎ পূর্বমুখী পদক্ষেপের নীতিতে পা দিয়েছে। দেশটি বাংলাদেশ, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, আসিয়ানভুক্ত দেশসমূহ এবং অস্ট্রেলিয়া ও জাপানের সঙ্গে অর্থনৈতিক ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোয় কাজ করছে। এ দিক থেকে চীনের বিআরআই ভারতের অ্যাক্ট ইস্ট নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক দেলওয়ার হোসেন । প্রথম আলোকে তিনি বলেন, ‘এর মধ্যে পড়ে বাংলাদেশকে ভারসাম্যের কূটনীতি ধরে রাখার চাপ সামলাতে হচ্ছে। আমাদের উচিত হবে অন্য রাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক সমস্যার ভেতর প্রবেশ না করা।’ কিন্তু চীনা সিল্ক রোড প্রকল্পের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার অর্থনৈতিক ও প্রাযুক্তিক সামর্থ্য ভারতের নেই। চীনের কাছাকাছি কোনো বিকল্প ভারতের দিক থেকে হাজিরও করা হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র-জাপান-অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতা কোনো বিকল্প প্ল্যাটফর্মেরও জন্ম দেয়নি। ড. দেলওয়ার ইস্ট এশিয়া স্টাডি সেন্টারেরও পরিচালক। তাঁর দৃষ্টিতে, ‘বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাহিদা পূরণের সামর্থ্য একমাত্র চীনেরই রয়েছে। ইতিমধ্যে চীনের প্রেসিডেন্ট ঢাকা সফর করে বিপুল ঋণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন। চীন বাস্তববাদী বলেই কূটনীতির মাধ্যমে সবাইকে উন্নয়নের অংশীদার করার কৌশল নিয়েছে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও আগের অবস্থান থেকে সরে উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছেন। জাপানও চীনের উদ্যোগকে এড়াতে পারেনি।’
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মনে করেন, ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড উদ্যোগ একই সঙ্গে সুযোগ ও ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। এই ঝুঁকির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক রয়েছে। যেহেতু বর্তমান সরকার রাজনৈতিকভাবে বৃহৎ প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, সেহেতু আরেকটি প্রথাগত বৃহৎ প্রতিবেশীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অস্বস্তি সৃষ্টি করতে পারে। আগে কোনো উদ্যোগে পাকিস্তান থাকলে ভারত অস্বস্তিতে থাকত, এখন চীন থাকলেও প্রতিক্রিয়া করে।’ দেবপ্রিয়ের মতে, ‘কাগজপত্রে ওয়ান বেল্ড ওয়ান রোড বা OBOR যত বড় হয়ে দেখা দিক, বাধাবিপত্তি আগামী দিনে বড় হবে। দেখতে হবে, এ থেকে কে কতটা উপকৃত হচ্ছে। অপরের লাভের জন্য কেউ তো ছাড় দেবে না।’
রাজনৈতিক ঝুঁকির পাশাপাশি অর্থনৈতিক ঝুঁকির দিকে মনোযোগ টেনে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ এখন বিনিয়োগ-ক্ষুধার্ত দেশ, সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ সংস্থান বড় বিষয়। অন্যদিকে, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশের দিকে যাওয়ার কারণে ক্রমান্বয়ে ঋণের সুদের রেয়াত পাওয়া আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যাবে। ভারত ও চীনের থেকে নেওয়া ঋণের বেলায়ও যথেষ্ট পরিমাণ স্বচ্ছতা নেই। এর ফলে দীর্ঘ মেয়াদে যে দায়দেনা সৃষ্টি হবে, তা বহনের সামর্থ্য আমাদের আছে কি না, তা ভাবা দরকার। বিআরআইয়ে যে বিপুল অবকাঠামো তৈরির কথা ভাবা হচ্ছে, তার অর্থনৈতিক ক্ষমতা আমাদের আছে কি না, তা ভাবা দরকার। যে ঋণ নিচ্ছি, তার দায়বহন ক্ষমতা (Debt-Sustenibility) আমাদের আছে কিনা, তাও উদ্বেগের বিষয়।’
অব্যাহত লোডশেডিং, শিল্পে গ্যাস-বিদ্যুতের ঘাটতি এবং প্রতিবছর যোগ হওয়া হাজারো শিক্ষিত বেকারের জন্য কর্মসংস্থান বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। ড. দেলওয়ার হোসেন মনে করেন, ‘তথা বিআরআইয়ে বাংলাদেশ যে সময়ে আগ্রহী হয়েছে, সে সময়টায় আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নও জোরদার হচ্ছে। এ উন্নয়নকে স্থায়িত্ব দিতে এমন আঞ্চলিক যোগাযোগজালে আমাদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে, যা গতিশীল ও বিশ্বায়িত। বাংলাদেশের যোগাযোগ ও জ্বালানি অবকাঠামো বিআরআইয়ের দ্বারা উপকৃত হবে। অর্থনীতির বর্তমান গতিবেগ ধরে রাখতে হলে অবকাঠামো দ্রুত উন্নত করতে হবে। অপেক্ষা করে থাকলে উন্নয়নের মহামুহূর্ত আমাদের হাতছাড়া হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।’
চীনা প্রেসিডেন্টের সফরকালে বাংলাদেশ ২৭টি চুক্তি সই করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে সময় বলেছিলেন, ‘আমাদের দুটি দেশ নতুন উচ্চতায় সহযোগিতা করছে।’ ইতিমধ্যে ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াটের পায়রা তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে একাধিক লেনের সুড়ঙ্গসড়ক, দাসেরকান্দি বর্জ্যনিষ্কাশন প্ল্যান্ট, পদ্মা সেতু, জাতীয় ডেটা সেন্টার নির্মাণকাজ চলছে। বিনৌবাহিনীর জন্য কেনা হয়েছে দুটি সাবমেরিন ও ছয়টি যুদ্ধজাহাজ। ২০১৭ সালকে ঘোষণা করা হয়েছে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রীবর্ষ।
এ ধরনের সহযোগিতা কত দূর যেতে পারে এবং ‘সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বের’ রাষ্ট্রীয় নীতি কীভাবে রক্ষা করা হবে? দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য যেমন মনে করেন, ‘বাংলাদেশের প্রতি বৃহৎ রাষ্ট্রের আগ্রহ যেমন মাহেন্দ্রক্ষণ, একই সময় তা নতুন ঝুঁকিও বয়ে আনছে। এ কারণেই আন্তর্জাতিক কোনো বলয়ে কীভাবে আমরা অংশ নেব, তা নিয়ে দেশের ভেতর রাজনৈতিক ঐকমত্য দরকার, গবেষণা দরকার। যে দেশে অভ্যন্তরীণ ঐক্য যত ভালো, বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক রচনায় তারা তত সফল। অথচ কী দেখলাম, ভারত বা চীনের কোনো বিষয়েই কি যথেষ্ট আলোচনা হলো? মন্ত্রিপরিষদ, সংসদ কিংবা সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে এসব নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে?’
তবে আশফাকুর রহমান মনে করেন, ‘বাংলাদেশে যে সরকারই আসুক, তারা এমন উদ্যোগে বাধা দেবে না। গভীর সমুদ্রবন্দরও সব সরকারই চাইবে, কারণ তা আমাদের খুবই প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী খুবই বিজ্ঞ। চীন বন্দর নির্মাণ করতে চাইলে ভারত আপত্তি করল। প্রধানমন্ত্রী বললেন, তোমারা দুজন মিলেই করো। আমি মনে করি, দরকার হলে, ভারত-চীন-নেদারল্যান্ডস মিলে কনসোর্টিয়াম করে করুন।’
সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সামরিক, অর্থনৈতিক চুক্তি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশ বৈশ্বিক ভূমিকা পালনে উৎসাহী হয়ে উঠছে। কিন্তু তার প্রস্তুতি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন বিশ্লেষকেরা। দেবপ্রিয়র ভাষায়, ‘দেখতে হবে এসব যেন আমাদের মৌল স্বার্থের পরিপূরক হয়। বর্তমানে সরকার একেকটা ইস্যুতে একেকভাবে পক্ষ নিচ্ছে। যেহেতু বর্তমান সরকার রাজনৈতিকভাবে ভৌগোলিক বৃহৎ প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, সেহেতু আরেকটি প্রথাগত বৃহৎ প্রতিবেশীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অস্বস্তি সৃষ্টি করতে পারে। যেমন চীনের কাছ থেকে সাবমেরিন কেনার কারণে ভারতের প্রতিক্রিয়া সামলাতে ভারতের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি করলাম। সব সময় এভাবে রাজনৈতিক ভারসাম্য সফলভাবে রক্ষা করা যায় না। কখনো কখনো সংকটের উদয় হতে পারে, যেমনটা প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের আগে হয়েছিল। বঙ্গোপসাগর ঘিরে পরাশক্তিগুলোর প্রতিযোগিতা মানসিক চাপ তৈরি করে রেখেছ, যা আমলে নেওয়া দরকার। এই অবস্থায় ঝুঁকি সামলানোই গুরুত্বপূর্ণ।’
তবে এই ঝুঁকি কমিয়ে আনার পথ হিসেবে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্কের যৌথতার কথা বলেন দেবপ্রিয়। বাংলাদেশ-মিয়ানমার যৌথভাবে ভারত-চীনের টানাপোড়েনকে প্রশমিত করতে পারে। তাঁর ভাষায়, ‘ভারসাম্য রক্ষা করেই বহুপক্ষীয় সেতুবন্ধের দেশ হতে পারে বাংলাদেশ।’
অবশ্য বিআরআইকে ভারসাম্য রক্ষারই কৌশল ভাবছেন আশফাকুর রহমান, ‘বিআরআই তো রাজনৈতিক কিছু না। এতে ৬৮টি দেশ জড়িত। এটা সফল হলে আমাদের যোগাযোগ অবকাঠামো ভালো হবে। যাতে সবাই একসঙ্গে এগোতে পারি। চীনের টাকা আছে, আমাদের দরকার উন্নয়ন-অবকাঠামো ও বাণিজ্যের প্রসার। চীনের সঙ্গে তো ভারতেরও ১০০ মিলিয়ন ডলারের ব্যবসা রয়েছে।’
বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক সুপ্রাচীন। ২ হাজার ৪০০ বছর আগে চীনারা বাংলার মাটিতে এসেছে। বৌদ্ধধর্ম বাংলা থেকেই চীনে প্রসারিত হয়েছে। চীনের মিং সাম্রাজ্যের সময় চীনের জাহাজ বাংলার উপকূলে এসেছে। পনেরো শতকের শেষে সুলতানি আমলে বাংলার বাণিজ্যিক জাহাজও চীনে নোঙর করেছে। ড. দেলওয়ার হোসেন চীনের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্যকে বহুপাক্ষিকতা বলে বর্ণনা করে বলেন, ‘চীন দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনৈতিক জটিলতার মধ্যে ঢুকতে চায় না বলেই দেখা গেছে। বাংলাদেশ-ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে তারা বাণিজ্যের জন্য বাধা মনে করে না। উন্নয়নমুখীনতাকে তারা যে গুরুত্ব দিচ্ছে, তা আমাদের অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষার জন্যও জরুরি। এই বৈশ্বিক উদ্যোগকে খাটো করে দেখলে আমরা দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হব। এক ঝুড়িতে সব ডিম রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ভারত যা–ই করুক, বিআরআই থেকে চীনকে বিচ্যুত করা যাবে না। ভারতের উদ্বেগ বাংলাদেশকে কূটনৈতিকভাবেই মোকাবিলা করতে হবে।’
পাক-চীন সম্পর্কের যে ধরন, বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক কিন্তু তেমন নয়। তাই পাক-চীন সম্পর্ককে ভারত যেভাবে দেখে, বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ককে সেভাবে দেখা যাবে না।
চীনের ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’: বাংলাদেশের উন্নয়নের সন্ধিক্ষণ ৩
নীল অর্থনীতিতে সামনের সারিতে বাংলাদেশ
চীনের অর্থনীতির অসুবিধা বাংলাদেশের চাহিদার পরিপূরক বা সুবিধা হয়ে দেখা দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক আন্তর্জাতিক নীতিগবেষণা প্রতিষ্ঠান লোয়ি ইনস্টিটিউটের গবেষক পিটার কাই (Peter Cai) বলছেন, ওয়ান বেল্ট, ওয়ান রোড বা ‘এক অঞ্চল এক পথ’ প্রকল্প আসলে চীনের অর্থনীতির জট কাটানোর মহাউদ্যোগ। এই জট তিনটি জায়গায়: প্রথমত, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা জিংজিয়াং প্রদেশকে এগিয়ে নেওয়া, দ্বিতীয়ত চীনের অলস পুঁজিকে বিশ্বব্যাপী লাভজনক বিনিয়োগে খাটানো এবং তৃতীয়ত, চীনের অতিরিক্ত শ্রম, কারখানা ও উৎপাদিত পণ্যকে বিদেশে রপ্তানি করা। ক্রমেই শ্লথ হয়ে আসা চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আগের গতিবেগে রাখতে চাইলে এই তিন জায়গায় তাদের সফল হতে হবে।
এর জন্য দরকার চীনের অর্থনীতির উন্নততর স্তরে আধুনিকায়ন। উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে কারখানাগুলোকে আরও গতিশীল করে আরও উচ্চতর পণ্য তৈরি করা ছাড়া চীনের পক্ষে পৃথিবীর ১ নম্বর অর্থনীতির দেশ হওয়া তথা আমেরিকার সমকক্ষ হওয়া কঠিন। তা ছাড়া চীনের কর্মক্ষম ও শ্রমিক জনসংখ্যাও কমতে থাকায় যন্ত্রনির্ভর উন্নত প্রযুক্তিতে তাদের যেতেই হবে। নতুন বাজার এবং কাঁচামালের নতুন উৎস পাওয়াও তাদের নয়া সিল্ক রোড প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ কাজে তাদের রয়েছে খুবই উন্নত যোগাযোগ প্রযুক্তি, উচ্চগতির ট্রেন ও রেলপথ নির্মাণের দক্ষতা এবং বিপুল পুঁজি। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) চেয়ে চীনের উদ্যোগে গঠিত এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের (এআইআইবি) তহবিল কয়েক গুণ বেশি-বাংলাদেশ ও ভারতও এই ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বর্তমান পৃথিবীতে সবেচেয়ে বেশি বৈদেশিক বিনিয়োগের রেকর্ডও চীনেরই দখলে।
সুতরাং চীনের অসুবিধা ও সুবিধা দুটোই বাংলাদেশের মতো নিম্নমধ্য থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ-আকাঙ্ক্ষী দেশের জন্য মানানসই হয়ে দেখা দিয়েছে। পোশাকশিল্প ও প্রবাসী শ্রমনির্ভর অর্থনীতি থেকে শিল্পায়িত অর্থনীতিতে উত্তরিত হতে হলে বাংলাদেশের দরকার বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক যোগাযোগের উপযুক্ত অবকাঠামো। চীন যেহেতু শিল্পায়নের পরের স্তরে যাত্রা করছে, সেহেতু তার অতিরিক্ত শিল্প ও অদরকারি প্রযুক্তি উন্নয়নশীল দেশে পাঠিয়ে দেওয়া তার দরকার। একসময় এভাবেই জাপানের দ্বিতীয় স্তরের প্রযুক্তি ও শিল্প দিয়ে চীন নিজের শিল্পায়ন ঘটিয়েছিল। বাংলাদেশের জন্যও একই মডেল কাজে দিতে পারে। আজকের বাংলাদেশ হতে পারে সে সময়ের চীন। বাংলাদেশ হতে পারে চীনা যন্ত্রপ্রযুক্তি ও চীনের ছেড়ে দেওয়া বাজারের লাভবান গ্রহীতা।
দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ চীন সাগরে জাপান ও আমেরিকার সঙ্গে বিরোধ থাকায় চীনের দরকার সামুদ্রিক বাণিজ্যের নতুন জলপথ। এর জন্য সবচেয়ে উপযোগী হলো বঙ্গোপসাগর তথা ভারত মহাসাগর। ইতিমধ্যে ভারত মহাসাগরের কাছে শ্রীলঙ্কার হামবানটোটা ও জিবুতি এবং আরব সাগরের তীরে পাকিস্তানের গদর বন্দর নির্মাণের কাজ চীন চালিয়ে যাচ্ছে।
ভারত মহাসাগর হলো একবিংশ শতাব্দীর কেন্দ্রীয় মঞ্চ। এর কিনারে রয়েছে সাহারা মরুভূমি থেকে ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ; রয়েছে সোমালিয়া, ইয়েমেন, ইরান ও পাকিস্তান। এ সাগর ঘিরেই চলছে গতিশীল বাণিজ্য, আবার একে ঘিরেই দানা বেঁধেছে বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ, জলদস্যুতা ও মাদক চোরাচালান। এর পূর্ব প্রান্তে বাস করে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার শত শত কোটি মুসলমান।
অন্যদিকে এর তীরেই বসবাস করে বিশ্বের বড় জনসংখ্যার কয়েকটি দেশ: ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া। এর ভেতর দিয়েই গেছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান জলপথ, এর তীরেই রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশগুলো। এই সমুদ্র প্রাকৃতিক সম্পদেও সমৃদ্ধ। বর্তমানে বছরে এই জলপথে ৯০ হাজার জলযান দিয়ে ৯ দশমিক ৮৪ বিলিয়ন টন বাণিজ্যিক পণ্য পরিবাহিত হয়। বিশ্বের ৬৪ শতাংশ তেলবাণিজ্য এই জলপথের ওপর নির্ভরশীল।
বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগর এবং চট্টগ্রাম বন্দর হলো এই বিশাল অর্থনৈতিক এলাকার প্রবেশমুখ। এই পথ দিয়ে চীনের ইউনান, জিংজিয়াং, ভারতের নিকটবর্তী প্রদেশগুলোসহ মিয়ানমার, নেপাল, ভুটানের পণ্য বিশ্ববাজারে প্রবেশ করতে পারবে, তেমনি বাইরের পণ্য এখান দিয়েই ওই সব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারবে। বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমারের মধ্যে অর্থনৈতিক করিডর (বিসিআইএম) এবং বঙ্গোপসাগরকেন্দ্রিক সহযোগিতা প্রক্রিয়া বিমসটেকের মতো কাঠামোর বাস্তবায়ন করা গেলে এর সুবিধা পুরো দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব দেশই পাবে। চট্টগ্রামে কিংবা মাতারবাড়ীতে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করা গেলে চট্টগ্রাম হতে পারবে এই বিশাল বাণিজ্যপথের প্রবেশমুখ।
ভারত মহাসাগরের এই বিপুল সম্ভাবনাকে বিআরআইয়ে জড়িত করতে হলে ভারতের সহযোগিতা চীনের লাগবেই। ইতিমধ্যে ভারত ও চীন অনেকগুলো আঞ্চলিক সহযোগিতা জোটের অংশীদার। এআইআইবি ব্যাংকেরও সদস্য এ দুটি দেশ। অন্যদিকে মিয়ানমার ও বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে আছে ভারত-চীনের মধ্যবর্তী সেতুবন্ধনকারী ভূমি হিসেবে। ভারতের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য ১০০ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানের কাশ্মীর ও ভারতের অরুণাচল নিয়ে ভারত-চীন দ্বন্দ্ব থাকলেও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে দেশ দুটি কেউ কারও প্রতিপক্ষ নয়। একুশ শতকে পৃথিবীর অর্থনীতিকে এশিয়াকেন্দ্রিক করতে হলে ভারত-চীনের উভয়ের উভয়কে প্রয়োজন হবে।
রাজনৈতিক অলংকারবহুল বক্তৃতার বাইরে দেখলে দেখা যায়, দুই দেশের ব্যবসা ও বাজার ক্রমেই আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলছে। সুতরাং ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতার চেয়ে অর্থনৈতিক স্বার্থের বড় হয়ে উঠতে কোনো বাধা নেই। আর দুই দেশের বিপুল দরিদ্র জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের তাগিদ এই সহযোগিতাকে অনিবার্য করে তুলছে। কোনো কোনো বিশ্লেষকের মতে, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান নিজের স্বার্থে চীনের সঙ্গে ভারতের টানাপোড়েন জিইয়ে রাখতে চাইছে।
বাংলাদেশ তাই দুদিক থেকেই লাভবান হতে পারে। চীনের নিম্ন প্রযুক্তির কারখানাগুলোকে বাংলাদেশে নিয়ে আসা, চীনা বিনিয়োগ শিল্প-জ্বালানি ও অবকাঠামো উন্নয়ন ঘটানো, সমুদ্রমুখী নীল অর্থনীতির সম্পূর্ণ সুবিধা নেওয়ার উপযোগী প্রশাসনিক-রাজনৈতিক ও কাঠামোগত বিনির্মাণ সম্পন্ন করার মধ্যেই এই সুযোগ নিহিত।
কিন্তু এই সুবিধার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা, তা বাস্তবায়নের কৌশল রপ্ত করা এবং যথাযথ কূটনৈতিক কর্মকাণ্ড দিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে সেগুলোকে সম্ভব করার প্রস্তুতি নিয়ে ঘাটতি রয়ে গেছে বাংলাদেশের।
এর জন্য বাংলাদেশের কূটনৈতিক দক্ষতা ও জ্ঞানসামর্থ্য বাড়াতে হবে। অথচ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ভারত বা চীনের জন্য আলাদা কোনো ডেস্ক নেই। গভীর জ্ঞানভান্ডার ও বিশেষজ্ঞের সাহায্য ছাড়াই দক্ষিণ এশিয়ার ভবিষ্যতের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ নিয়ে ফেলছে।
চীনের ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’: বাংলাদেশের লাভক্ষতি ৪
সুযোগ আসছে, নিতে পারবে কি বাংলাদেশ?
বহুজাতিক ব্যাংক স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক (এসসিবি) ঢাকায় নিয়মিতভাবে ‘চায়না নাইট’ বা চীন-রজনীর আয়োজন করছে। ব্যাংকটির মূল দপ্তরে চালু করা হয়েছে বিশেষ চীন ডেস্ক। বাংলাদেশের সঙ্গে চীনা গ্রাহকদের যোগাযোগ সহজ করতে চীনাভাষী রিলেশনশিপ ম্যানেজার আছেন সেখানে। ব্যাংকটি চীনা ভাষায় বইও প্রকাশ করেছে। নতুন যেসব চীনা কোম্পানি বাংলাদেশের বাজারে আসবে, বইটি হবে তাদের গাইড। চীনের সিল্ক রোড প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশে সম্ভাব্য চীনা বিনিয়োগ থেকে ব্যবসায়িকভাবে লাভবান হওয়াই এসবের উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে এসসিবি জ্বালানী-বিদ্যুৎ ও অবকাঠামো খাতে চীনা বিনিয়োগের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। টেলিকম খাতেও চীনের এক্সিম ব্যাংকের বিনিয়োগসঙ্গী ছিল এসসিবি। বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্পে জড়িত হতে প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশে কর্মরত আরো কয়েকটি ব্যাংক।
অথচ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিংবা পরিকল্পনা কমিশনে নেই কোনো বিশেষ চীন ডেস্ক। এখন পর্যন্ত এ প্রকল্প বিষয়ে পাওয়া যায়নি সামগ্রিক নীতিগত দলিল। অথচ চীন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য অংশীদার। মূল-চীন বলে পরিচিত গণপ্রজাতন্ত্রী চীন এবং হংকং ও তাইওয়ানই বাংলাদেশের সরাসরি বিনিয়োগকারী (এফডিআই) বড় দেশ। ২০১৫ সালে এর পরিমাণ ছিল ১৯৩ মিলিয়ন ডলার।
বাংলাদেশ ও চীন ইতিমধ্যে আমব্রেলা চুক্তির অধীনে বিনিয়োগ শক্তিশালী এবং উৎপাদনক্ষমতা বাড়ানোর পদক্ষেপ নিয়েছে। অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে অবকাঠামো, জ্বালানি ও শক্তি, যোগাযোগ ও পরিবহন এবং চট্টগ্রামে চীনা অর্থনৈতিক ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল অঞ্চল (ইপিজেড) প্রতিষ্ঠাসহ ২৫টি প্রকল্প। এসবে মোট বিনিয়োগ করা হবে ২৪ বিলিয়ন ডলার। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বাংলাদেশের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও হেড অব গ্লোবাল ব্যাংকিং নাসের এজাজ বিজয় প্রথম আলোকে বলেন, ‘চট্টগ্রাম ও মোংলার দুটি সমুদ্রবন্দরের আধুনিকীকরণ ও সামর্থ্য বাড়ানো এবং পায়রা ও সোনাদিয়ায় প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্রবন্দর অর্থনীতিতে বহুমাত্রিক প্রভাব ফেলবে। রাজস্ব যেমন বাড়বে, তেমনি বাংলাদেশের অনুকূলে বাণিজ্যিক ভারসাম্যও বাড়াবে। এসব বন্দর ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক সমুদ্র পরিবহনের সঙ্গে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের বর্ধনশীল সামুদ্রিক বাণিজ্যকে তাল মেলাতে সাহায্য করবে। চীনের জন্য বিশেষ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) ৭৫ হাজার থেকে এক লাখ বাংলাদেশির সরাসরি কর্মসংস্থান হবে। এই ইপিজেডে ১৫০ থেকে ২০০টি শিল্প ইউনিটে জাহাজ নির্মাণ, ওষুধ, ইলেকট্রনিক, কৃষিভিত্তিক, তথ্যপ্রযুক্তি, শক্তি ও টেক্সটাইল ও টেক্সটাইল যন্ত্রাংশ তৈরি করা হবে। এভাবে ভূরাজনৈতিক সুবিধা ব্যবহার করে আমরা ভারত মহাসাগরের আঞ্চলিক প্রবেশমুখের সুবিধা পাব।’
বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের ১৫.৯ শতাংশের অংশীদার চীন। মূলত রপ্তানি হয় পোশাক (৮৪ ভাগ), চামড়া, পাট (পাট ও পাটজাত পণ্য) ও হিমায়িত খাদ্য। বিআরআইয়ের মাধ্যমে চীন-মিয়ানমারের সঙ্গে কানেকটিভিটি বা সংযোগ নিবিড় হলে বাণিজ্যের আওতাও অনেক বাড়বে। বর্তমানে ৪ হাজার ৭০০ বাংলাদেশি পণ্য চীনের শুল্কসুবিধা পায়। চামড়াজাত পণ্য ও তামাকসহ আরও ১৭টি পণ্যও যোগ হবে এই তালিকায়। বিআরআই প্রধান প্রধান বাংলাদেশি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুযোগ আরো বাড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে। গত কয়েক বছর যাবৎ চীনের কাছ থেকে পোশাকশিল্প পণ্যের জন্য এই সুবিধা বাংলাদেশ চেয়ে আসছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের বিপুল বাণিজ্যঘাটতি কি তাতে কমবে? যেখানে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানির হয় ৬৬৩.৪ মিলিয়ন ডলারের পণ্য, সেখানে আমদানি হয় ৯.৬৬২.৪ মিলিয়ন ডলারের পণ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক দেলওয়ার হোসেন মনে করেন, ‘বাজার অর্থনীতিতে আমদানিও গুরুত্বপূর্ণ। চীন থেকে যা আমদানি করছি, তা আমাদের শিল্পায়নকে এগিয়ে দিচ্ছে। জাপান, কোরিয়া বা জার্মানি থেকে আমদানি করা তো আরও ব্যয়বহুল।’
চীনের অর্থনীতির রূপান্তর থেকে বাংলাদেশের সুবিধা নেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘চীনে হোয়াইট কলার শ্রমিক কমে যাচ্ছে, শ্রমঘন শিল্প থেকে তারা সরে আসছে, গার্মেন্টস কারখানা কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে তাদের মধ্যবিত্তের আয়তন বড় হচ্ছে। চীনের ছেড়ে দেওয়া এসব শিল্প যদি বাংলাদেশে আনা যায় এবং চীনারা যদি এসবে বিনিয়োগ করে, তাহলে বহির্বিশ্বে এসব পণ্যের বাজারটাও আমরা পেতে পারি। তাদের নিজস্ব বাজারের জন্যও তারা আমাদের দেশে বিনিয়োগ করতে পারে।’
ঢাকা চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি আবুল কাশেম খান মনে করেন, বাংলাদেশের দুই পাশে দুই বৃহৎ অর্থনীতির উত্থান থেকে সুবিধা নিতে আঞ্চলিক কানেকটিভিটি বাড়ানো দরকার। তাঁর ভাষায়, ‘বাংলাদেশ চীন-ভারতের মধ্যে পণ্য সরবরাহ এবং উৎপাদন তথা ম্যানুফ্যাকচারিং কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠতে পারে। চীনা প্রেসিডেন্টের সফরের সময় যে ২৪ বিলিয়ন ডলারের অঙ্গীকার করা হয়েছে, সেটাই তো বাংলাদেশে বিআরআইয়ের দিকনির্দেশনা। কিন্তু তার জন্য বিবিআইএম, বিসিআইএম, বিমসটেক ও সার্কের মতো আঞ্চলিক যোগাযোগ কাঠামোকে সক্রিয় করা দরকার।’
তিনি মনে করেন, ‘আমরা আইটি থেকে শুরু করে ভারী শিল্প, ইলেকট্রনিক ও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পদ্রব্য থেকে শুরু করে শ্রমঘন শিল্পগুলো বাংলাদেশে টানতে পারি। কিন্তু বাস্তবায়নটা দ্রুততর করা দরকার। জ্বালানি গ্যাস, বিদ্যুৎ এবং সড়ক ও বন্দরের কানেকটিভিটি দ্রুত সম্পন্ন না হলে সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে।’ বাণিজ্যঘাটতি বিষয়ে এই শিল্পোদ্যোক্তা মনে করেন, ‘অল্প সময়ে বাণিজ্যঘাটতি কমবে না। এর জন্য আমাদের দক্ষতা, প্রযুক্তি ও পরিকল্পনাগত অনেক উন্নতির দরকার আছে।’
আমরা কি আমদানি ব্যবসা করব নাকি উৎপাদন বাড়িয়ে দেশে ও বিদেশে বাজার তৈরি করব? এমন শিল্পনীতি নিতে হবে, যা দেশে ভোগ ও বিদেশে রপ্তানি বাড়াবে। আমাদের বাণিজ্যিক যোগাযোগজালকে উৎপাদনমুখী যোগাযোগজালে পরিণত করতে হবে।
চীনে নিযুক্ত সাবেক বাংলাদেশি কূটনীতিবিদ আশফাকুর রহমান মনে করেন, ‘সিঙ্গাপুরের সমৃদ্ধি দাঁড়িয়ে আছে দুটি জিনিসের ওপর: বিমানবন্দর আর সমুদ্রবন্দর। বিআরআই থেকে সুফল নিতে হলে আঞ্চলিক যোগাযোগ ও মুক্তবাজারের উদারতা দেখাতে হবে।’
বাণিজ্যিক উদারতা থেকে সব দেশ লাভবান হয়নি বলে জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক রাশেদ আল মাহমুদ তীতুমীর। তিনি বলেন, ‘উদারতাবাদ ও মুক্তবাজারই যদি উন্নতির সোপান হতো, তাহলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বাড়েনি কেন? আমাদের বাণিজ্য চীনের সঙ্গে, ইউরোপের সঙ্গে, আমেরিকার সঙ্গে; কিন্তু নিজেদের মধ্যে নয়। নতুন বাজার সৃষ্টি হলেও উন্নয়নশীল দেশের নিজস্ব পুঁজি সৃষ্টি হয়নি। বিদেশি ব্যবসায়ীদের মুনাফার একটি অংশ স্থানীয় পুঁজি হিসেবে বিনিয়োজিত হয়নি। পশ্চিমা বিশ্বায়নের সুফলও পেয়েছে গুটিকয় দেশের সীমিত একটি অংশ। অন্যদিকে উন্নত ও অনুন্নত উভয় দেশেই বৈষম্য বেড়েছে। প্রতিক্রিয়ায় ডোনাল্ড ট্রাম্প কিংবা ব্রেক্সিটের মতো অনুদার নীতি জনপ্রিয় হচ্ছে। আমরা বিকৃত বিশ্বায়ন চাই না। এ অবস্থায় চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ নতুন ধরনের বহুত্ববাদ বা মাল্টিল্যাটারিলজমের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আমরা সত্যিকার উদারতার পক্ষে, যেখানে উৎপাদনের উপকরণ, পুঁজি ও প্রযুক্তির সুষম চলাচল ঘটবে।’
অর্থনীতিবিদ তিতুমীর বলেন, ‘আমাদের ঠিক করতে হবে, আমরা কি আমদানি ব্যবসা করব নাকি উৎপাদন বাড়িয়ে দেশে ও বিদেশে বাজার তৈরি করব? এমন শিল্পনীতি নিতে হবে, যা দেশে ভোগ ও বিদেশে রপ্তানি বাড়াবে। আমাদের বাণিজ্যিক যোগাযোগজালকে উৎপাদনমুখী যোগাযোগজালে পরিণত করতে হবে। চীনের ছেড়ে দেওয়া কারখানা ও পুঁজি আমাদের এখানে পুনঃস্থাপন ও পুনঃ বিনিয়োগের রূপরেখাটা কী হবে? পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মিলিয়ে সমন্বিতভাবে চিন্তা ও কাজ করতে হবে।’
উন্নয়নকে টেকসই ও সবার জন্য করার জন্য দরকারি ও উপযুক্ত শর্তের ওপর জোর দেন তীতুমীর। তিনি বলেন, ‘স্থানীয় শ্রম, পুঁজি ও প্রযুক্তিকে গতিশীল করতে হবে। ভারত ২ বিলিয়ন ডলার বা চীন ২৪ বিলিয়ন ডলারের যে ঋণ দিচ্ছে, একে টেকসই ঋণ ব্যবস্থাপনা বলা যায় না। একসময় এসব ঋণ শোধ করা কঠিন হয়, তখন আরও ঋণ নিতে হয়। এ ধরনের ঋণ-অর্থায়নের কারণেই গ্রিস ও ইতালি বিরাট সমস্যায় পড়েছিল। বর্তমানে ঋণের সুদ-আসল ফেরত দিতেই বাজেটের বড় অংশ চলে যাচ্ছে। এমন বিদেশি বিনিয়োগ হতে হবে, যেখানে লাভ-লোকসান দুটিই ভাগ হবে। একে বলা হয়, ঝুঁকি-বণ্টনমূলক অর্থায়ন কাঠামো। আমরা চাইব, কানেকটিভিটি ও বিনিয়োগ দেশীয় পুঁজি গঠনে ভূমিকা রাখবে।’
চীনের উদ্যোগে নয়া বিশ্বায়নকে তাই সৃজনশীলভাবে ধারণ করার কথা বলেন অর্থনীতিবিদ তীতুমীর। ‘শুধু খণ্ড খণ্ড প্রকল্প জোড়া লাগানো আর বিরাট আকারে ঋণ-তহবিল গঠন করলেই উন্নয়ন হয় না, চিন্তাকাঠামো এবং কাজের ধারাই বদলে ফেলা দরকার। তা না হলে বর্তমানের কর্মসংস্থানহীন প্রবৃদ্ধির বর্তমান মডেল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে’, বলেন তিনি।
বিআরআই প্রকল্পে লাভবান হওয়ায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বিষয়ে কোনো কোনো বিশ্লেষক প্রশ্ন তুলছেন। দক্ষতাঘাটতি পূরণে বিদেশি কর্মী আনতে হচ্ছে অনেক খাতেই। তাতে করে রেমিটেন্সপুষ্ট বাংলাদেশ হয়ে পড়েছে রেমিটেন্স পাঠানোর দেশে। স্থানীয় শ্রমদক্ষতা বাড়ানোর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। বিদেশি ঋণ ও বিনিয়োগের মধ্যে ভারসাম্য আনাও জরুরি। চীনের বিআরআই শুধু রাষ্ট্রীয় বিষয় নয়। সরকার বদলালেও বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ন রাখার কাঠামোটা কী হবে? যুক্তরাষ্ট্র-জাপান, যুক্তরাষ্ট্র-কোরিয়া কিংবা চীন-পাকিস্তান সম্পর্ক জনগণের স্তরেও আস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে। সুযোগ দেওয়ার বিষয় নয়, নেওয়ার বিষয়। তার জন্য সামর্থ্য ও যোগ্যতা বাড়ানোর দায়টা বাইরের কারোর নয়, বাংলাদেশেরই।
Writer: Faruk Wasif
Series posts @ Daily Prothom Alo
